অনুবাদক: মনিরুল ইসলাম
অনুবাদকের কথা
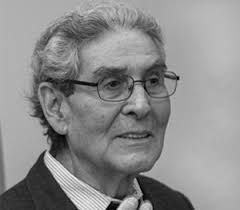
উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কিহানোর (Aníbal Quijano) ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। রাজনৈতিকভাবে ঔপনিবেশিক পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটলেও উপনিবেশিক ব্যবস্থা–যে ঠিকই কার্যকর থাকে, অপরাপর তাত্ত্বিকদের এই প্রস্তাবনার সঙ্গে কিহানো একমত পোষণ করলেও এর জন্য তিনি কেবল মনোজগতে আশ্রয় নেওয়া ঔপনিবেশিক মন্ত্রকেই দায়ী করেন না। এই প্রশ্নে আরও সুবিন্যস্ত জবাব তার আছে। তিনি বলেন উপনিবেশিকতার কথা। এই কথা বলার সময় ‘উপনিবেশিকতা’ প্রত্যয়টিকে তিনি উপনিবেশবাদ থেকে আলাদা করে নেন। তার ভাবনায়, উপনিবেশবাদ নির্দেশ করে এক–ধরনের রাজনীতিক–আর্থনীতিক সম্পর্ক যেখানে একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে অপর আরেকটি কর্তৃত্ববাদী দেশের উপর যা কর্তৃত্বপরায়ণ দেশটিকে একটি সাম্রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলে। অন্যদিকে, উপনিবেশিকতা হলো উপনিবেশায়নের ফলে সৃষ্ট হওয়া দীর্ঘস্থায়ী এক ক্ষমতাবিন্যাস যা ঔপনিবেশিক প্রশাসনের আওতা–বহির্ভূত সংস্কৃতি, শ্রম, আন্তঃবিষয়ী সম্পর্ক ও জ্ঞানোৎপাদনকে সংজ্ঞায়িত করে। এই দুইয়ের সম্পর্ক হলো—উপনিবেশবাদকে টিকিয়েই রাখে উপনিবেশিকতা। এবং এটি সুপ্ত থাকে বই–পুস্তকে, বিদ্যায়তনিক তৎপরতায়, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে, প্রাত্যহিক বোঝাপড়ায়, সাধারণের আত্ম–ভাবনায়, আত্মবোধের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ও অন্যান্য আধুনিক যাপনাভিজ্ঞতায়। অর্থাৎ, আধুনিক বিষয়ী হিসেবে আমরা যেন প্রতিদিন ও প্রতিটি মুহূর্ত উপনিবেশিকতার মধ্যেই দম নিই। ফলে, উপনিবেশিকতা কোনো উপনিবেশিক সম্পর্কের সরল পরিণতি বা অবশিষ্ট নয়; তার নির্মাণ ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠার নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত ও সমাজৈতিহাসিক বৃত্তান্ত রয়েছে (Maldonado-Torres, 2010 : 97)।
কিহানো লক্ষ করেছেন–যে আমেরিকা দখলের আগেকার আমলের উপনিবেশবাদ কোনো বৈশ্বিক শক্তির ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ ছিলো না। সেইক্ষেত্রে, আমেরিকার উপনিবেশায়ন ছিলো ব্যতিক্রম—তা নির্মাণ করেছে নতুন ধরনের এক ক্ষমতা কাঠামো। এবং বিশেষ এই ক্ষমতাসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনে পৃথিবীর মানুষ সংজ্ঞায়িত হয়েছে বর্ণবাদী মানদণ্ডে; ‘পুঁজিবাদ’ শিরোনামে পুনর্বিন্যাসিত হয়েছে গোটা দুনিয়ার শ্রমপরিসর; জ্ঞানোৎপাদনের ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছে বিষয়ী–বিষয় নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ, গড়ে উঠেছে উপনিবেশিকতা। তিনি এর নাম দেন—ক্ষমতার উপনিবেশিকতা। ক্ষমতার উপনিবেশিকতায় ইউরোকেন্দ্রিক যুক্তির আশ্রয়ে গড়ে ওঠে বিশেষ কিসিমের যৌক্তিকতাও, যা আপনকার প্রাদেশিক ও উপনিবেশিক চরিত্র গোপন করে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার ঝান্ডা উড়িয়ে হাজির হয়েছে সর্বজনীন রূপে; ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অভিজ্ঞতা ও ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বে উৎপাদিত জ্ঞানকে সেখানে পেশ করা হয়েছে গোটা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বলে। যার দরুন, ইউরোকেন্দ্রিক জ্ঞানতত্ত্ব হয়ে ওঠেছে এক ও অদ্বিতীয়। যে জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্গত উপনিবেশিকতা আড়াল হয়েছে আধুনিকতার বয়ান দিয়ে। কিহানোর এই সূত্র ধরেই কিহানো–প্রভাবিত লাতিন আমেরিকার অপরাপর তাত্ত্বিকেরা আধুনিকতা ও উপনিবেশিকতাকে প্রতিপন্ন করেন একই মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ। গঠনগতভাবেই যার একটি আড়াল করে অপরটিকে। আধুনিকতা যাদের ভাবনায় উপনিবেশিকতারই নামান্তর। মাঝখানে স্ল্যাশ ব্যবহার করে এই দুইটিকে তারা বিজড়িত করে তোলেন। লেখেন—আধুনিকতা/ উপনিবেশিকতা (Mignolo, 2018 : 141)। গড়ে তোলেন ‘আধুনিকতা/ উপনিবেশিকতা গবেষণা প্রকল্প’। কিহানো এই উপনিবেশিকতাকে নস্যাৎ করতে বি–উপনিবেশায়ন হিসেবে প্রস্তাব করেন জ্ঞানতাত্ত্বিক পুনর্গঠন, যা ইউরোপীয় সর্বজনীনতার দাবির পরিবর্তে প্রস্তাব করে কতিপয় সর্বজনীনতা, যা ইউরোপীয় জ্ঞানতত্ত্বের জবরদস্তির ফলে চাপা–পড়া অপরাপর জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবকে স্বাগত জানায়; কেবল ইউরোকেন্দ্রিক যৌক্তিকতাই নয়—যা প্রস্তাব করে অপরাপর ধরনের যৌক্তিকতাও।
কিহানোর বিদ্যাবত্তাকে মোটামুটি তিনটি পর্বে বেশ ভালো মতো ব্যাখ্যা করা যায়। প্রতিটি পর্বই যেখানে নির্ভরশীলতার ব্যাপক ধারণাটিকে পাঁক খেয়ে বিকশিত হয়েছে, যা রাজনীতিক–আর্থনীতিক বোঝাপড়া থেকে তাকে পৌঁছে দেয় সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিবেচনায়। ষাট ও সত্তর দশকের নির্ভরশীলতা তত্ত্ব (dependency theory), আশির দশকের আধুনিকতা, ইতিহাসতত্ত্ব, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়–বিতর্ক এবং নব্বই দশকের ও এখনকার বি–উপনিবেশিক তত্ত্বে কিহানোর মৌলিক অবদান রয়েছে। উপনিবেশবাদকে তিনি দুর্দান্ত এক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। যার ফলে, কেবল লাতিন আমেরিকা নয়, উত্তর–ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও বি–উপনিবেশিক অধ্যয়নেও তার প্রভাব তৈরি হয়েছে। অবশ্য একইসঙ্গে, কতগুলো ক্ষেত্রে তার চিন্তা পুনর্মূল্যায়নেরও দাবি রাখে—বিশেষ করে বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বের জায়গা থেকে। প্রথমত, কিহানোর চিন্তায় ক্ষমতার উপনিবেশিকতা সর্বজনীন ছেদক রূপে হাজির হয়। অর্থাৎ, তা সমাজের সকল সম্পর্ককেই যেন ছেদ করে যায়। মিগনোলো যাকে টেনে ‘ক্ষমতার উপনিবেশিক মাতৃকা’ পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন (Mignolo, 2018 : 142)। এখন তাই যদি হয়, ক্ষমতার উপনিবেশিকতা তো তাহলে কিহানোর চিন্তাকেও ছেদ করে গিয়েছে। ফলে, কোন চিন্তাকাঠামোয় দাঁড়িয়ে তিনি ইউরোপীয় যৌক্তিক চিন্তাকাঠামোর বিকল্প প্রস্তাব করেছেন? আর উপনিবেশিকতা যদি সর্বজনীন ছেদক না–ই হয়ে থাকে, অর্থাৎ কিছু সম্পর্ককে তা যদি ছেদ করতে না–ই পারে, নিজেই যদি সকল ক্ষেত্রে টিকে থাকতে না পারে, উপনিবেশবাদকেই বা তা টিকিয়ে রাখবে কীভাবে? উপনিবেশিকতা কি তাহলে গোটা সমাজে কার্যকর নয়? দ্বিতীয়ত, তার আলোচনায় উপনিবেশিকতা বৈশিষ্ট্যগতভাবে অপরিবর্তনীয় রূপে সংজ্ঞায়িত। কিন্তু মানুষের সমাজ তো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে, রূপান্তরশীল সমাজের ক্ষেত্রে ক্ষমতার উপনিবেশিকতার নিয়ত পরিবর্তনশীলতা তাহলে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? তৃতীয়ত, উপনিবেশিকতাকে যদি বি–উপনিবেশিকতা দিয়ে নস্যাৎ করতে হয়, তাহলে কিহানোর চিন্তা তো ইউরোপীয় বৈপরীত্য জোড় অতিক্রম করতে পারলো না। অথবা তিনি যদি ইউরোকেন্দ্রিক সর্বজনীনতার বিকল্প হিসেবে, সহনশীল কায়দায়, কেবল কতিপয় সর্বজনীনতার প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত দেন, সেক্ষেত্রেও তাহলে ইউরোপীয় বিনির্মাণ তত্ত্বের চৌহদ্দি তিনি পেরোলেন কই? আসলে প্রশ্নগুলো কেবল কিহানোকে সমালোচনা করার জন্যই নয়, বরং ভালো মতো তাকে পাঠ করার জন্যই। উদ্দেশ্য—বি–উপনিবেশায়ন তত্ত্বে তার অবস্থানকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা। এরচেয়েও বড়ো কথা, তার ভাবনাকে আশ্রয় করে বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্ব সম্পর্কেই নানান মাত্রায় চিন্তা করা।
১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর পেরুর ইয়াঙ্গে (Yungay) প্রদেশের ইয়ানামা (Yanama) জেলায় কিহানোর জন্ম। পেরুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব স্যান মার্কুস (National University of San Marcos) থেকে—১৯৬৪ সালে—তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সেখানেই সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সিনিয়র লেকচারার পদে আসীন ছিলেন। অতি সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের বিংহামটন ইউনিভার্সিটির (Binghamton University) সমাজবিদ্যার অধ্যাপক হয়েছিলেন। এছাড়া সমাজবিজ্ঞানের অতিথি অধ্যাপক (visiting professor) হিসেবে দুনিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন, প্যারিসের মিজোঁ দে সায়েন্সেস দু লোম্মা (Maison des Sciences de l’Homme), ইউনিভার্সিটি অব সাও পাউলো, ইউনিভার্সিটি অব পুয়ের্তো রিকো, ইউনিভার্সিটি অব হ্যানোভার, ফ্রি ইউনিভার্সিটি অব বার্লিন, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ইকুয়েডর, ন্যাশনাল অটোনমাস ইউনিভার্সিটি অব মেক্সিকো, উনিব্যারসিদাদ দে চিলি (Universidad de Chile), লাতিন আমেরিকান স্কুল অব ইকোনমিক্স ও জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। তার প্রথম দিককার চিন্তায় কেউ কেউ উদারনৈতিক ধারার তাত্ত্বিক হোসে মেদিনা এচাবারিয়া (José Medina Echavarría)) ও মার্কসীয় তাত্ত্বিক হোসে কার্লোস মারিআতেগির (José Carlos Mariátegui) প্রভাব লক্ষ করেছেন (Gandarilla, García-Bravo & Benzi, 2021 : 204) । তার গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহের মধ্যে রয়েছে : ‘Paradoxes of Modernity in Latin America’ (1989), ‘Coloniality and Modernity/Rationality’ (1991), ‘Americanity as a Concept, or the Americas in the Modern World-System’ (1992), ‘Modernity, Identity and Utopia in Latin America’ (1993), ‘Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America’ (2000), ‘Questioning “Race”’ (2007)। লাতিন আমেরিকার বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রভাবশালী এই তাত্ত্বিককয়েক বৎসর আগে—২০১৮ সালের ৩১ মে—পেরুর রাজধানী লিমায় (Lima) মৃত্যুবরণ করেন।
অনূদিত এই বাংলা প্রবন্ধটি সোনিয়া থেরবর্নকৃত (Sonia Therborn) অনুবাদের অনুবাদ হলেও Perú Indígena –সংস্করণটিও এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সুবাদে বলে ফেলা যায়, মূল পেরু–সংস্করণের সঙ্গে কিন্তু থেরবর্ন অনূদিত Cultural Studies পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির বেশ কিছু জায়গায় ভিন্নতা আছে। কোথাও কোথাও রয়েছে বাক্যাংশের অমিল বা অনুপস্থিতি। যেমন ‘‘জনগোষ্ঠী’ (Race) ও ক্ষমতার উপনিবেশিকতা’ নামের পরিচ্ছেদটিই পেরু–সংস্করণে নেই—যা থেরবর্নের অনূদিত প্রবন্ধে রয়েছে। তবে দুইয়ের এই ভিন্নতাটুকু মূল প্রবন্ধের সঙ্গে অনূদিত প্রবন্ধটির ভাবগত কোনো সংঘর্ষ তৈরি করে না। এইসব ক্ষেত্রে থেরবর্নের ইংরেজি অনুবাদটিকে মূলত আশ্রয় করলেও Perú Indígena–র মূল রচনাটির ভিত্তিতেও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—অবশ্য তা খুবই সামান্য। স্প্যানিশ না–জেনেও উন্নত সফটওয়্যারের বদৌলতেই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। এবং ভাবানুবাদ নয়—এখানে মূল পাঠের অনুগামী থাকার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা ব্যয় করা হয়েছে। তবু অসতর্কতাবশত তুচ্ছ ভুলের জন্য আগাম ক্ষমাপ্রার্থী, ভবিষ্যতে যা সংশোধনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।
মূল প্রবন্ধ
যে ভূখণ্ডটাকে আমরা এখন লাতিন আমেরিকা নামে চিনি, একসময় এই এলাকাটির সমাজ ও সংস্কৃতিকে জবরদখল করার মাধ্যমে নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিলো, যা তার সর্বোচ্চ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছায় তারও ৫০০ বছর পর, যখন একটি বিশ্বশক্তি পুরো পৃথিবীটাকেই গ্রাস করে ফেলেছে। এই প্রক্রিয়ায় ইউরোপের ক্ষুদ্র একটি অংশের তত্ত্বাবধানে ও ফায়দার জন্য—সর্বোপরি এর শাসকগোষ্ঠীগুলোর স্বার্থে—পৃথিবীর সম্পদরাশির প্রতি এক আগ্রাসী মনোভাবের জন্ম হয়েছিলো। যদিও নিপীড়িত অধিবাসীদের প্রতিরোধের ফলে কখনো–সখনো এই ব্যবস্থা পরিমার্জিত হয়েছে, তবুও তা এগিয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতেই। কিন্তু এখন, সংকটের এই বর্তমান কালে, এই মনোভাব বাস্তবায়িত হচ্ছে নিত্যনতুন সংবেগে—খুবসম্ভব অধিকতর আগ্রাসী উপায়ে ও আরও বিস্তৃত বৈশ্বিক পরিসরে। ‘পশ্চিম’ ইউরোপীয় আধিপত্যবাদীরা ও তাদের ইউরো–নর্থ আমেরিকান বংশধরগণ এখনও প্রধান সুবিধাভোগী, সেইসঙ্গে [যুক্ত হয়েছে] প্রাক্তন ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো ব্যতীত বিশ্বের অ–ইউরোপীয় অংশ, প্রধানত জাপান, বিশেষত তার শাসকগোষ্ঠী। লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার শোষিত ও নিপীড়িতরাই প্রধান শিকার।
সবগুলো মহাদেশেই বিজিতদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের দ্বারা সরাসরি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এক আধিপত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। আধিপত্যের এই সম্পর্কই সুনির্দিষ্টভাবে ইউরোকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদ নামে পরিচিত। রাজনীতিকভাবে, বিশেষত আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য চেহারায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উপনিবেশিক আধিপত্যের হার হয়েছে। আমেরিকা ছিলো সেই পরাজয়ের পয়লা দৃশ্য। পরবর্তীকালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, [যুক্ত হয়] আফ্রিকা ও এশিয়া। এভাবে, কতিপয় পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ কর্তৃক অপরের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ফলানোর আনুষ্ঠানিক কায়দাস্বরূপ যে ইউরোকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদ তা এক অতীত প্রসঙ্গ [হয়ে যায়]। তারই উত্তরসূরি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, বাইরে থেকে [দাদাগিরি] আরোপণের পরিবর্তে, ক্ষমতায় অসমভাবে সন্নিবিষ্ট দেশগুলোরই প্রভাবশালী দলসমূহের (‘সামাজিক শ্রেণি’ বা ‘গোষ্ঠী’) মধ্যেকার সামাজিক স্বার্থের একটি সংস্থা।
যাইহোক, উপনিবেশিক সেই নির্দিষ্ট ক্ষমতাকাঠামোই সুনির্দিষ্ট–সব সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিয়েছিলো যা পরবর্তীকালে—সময়, বাহক ও অধিবাসীদের সংশ্লিষ্টতা সাপেক্ষে—‘জাতিগত’, ‘গোষ্ঠীগত’, ‘নৃ–তাত্ত্বিক’ ও ‘জাতীয়’ হিসেবে [বর্গে] গ্রথিত হয়। এইসব আন্তঃবিষয়ী নির্মাণসমূহ, ইউরোকেন্দ্রিক আধিপত্যের ফসলরাজি, ইতিহাস সাপেক্ষ অর্থের বদলে এমনকি গণ্য হয়েছে ‘নৈর্ব্যক্তিক’, ‘বৈজ্ঞানিক’ বর্গ (categories)* হিসেবে। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক প্রপঞ্চরূপে, ক্ষমতার ইতিহাস হিসেবে নয়। এই ক্ষমতাকাঠামোর নির্মাণশৈলীর ভেতরেই সক্রিয় ছিলো, এবং এখনও আছে, শ্রেণি বা ভূসম্পত্তির অপরাপর সামাজিক সম্পর্কসমূহ।
আসলে, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে শোষণ ও দমনের প্রধান রেখাটিকেই আমরা যদি লক্ষ করি—বর্তমান বিশ্বক্ষমতার মূল রেখাটিকে—অর্থাৎ, পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সম্পদ ও শ্রম–পরিসরের বণ্টন[কে], তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে–যে শোষিত, নিগৃহীত ও বঞ্চিত জনসংখ্যার অধিকাংশই ‘জাতিগোষ্ঠী’, ‘নৃ–সম্প্রদায়’ বা ‘জাতীয়’ পরিচয়ে চিহ্নিত, যাদের অধিকাংশই উপনিবেশিত এবং সেই আমেরিকা দখলের সময় থেকেই যারা এভাবে চিহ্নিত ও বর্গীকৃত হয়ে আসছে।
অনুরূপভাবে, রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের পরিসমাপ্তি সত্তে¡ও ইউরোপীয়—‘পশ্চিমা’ও বলা হয়ে থাকে—সংস্কৃতির সঙ্গে অপরাপর সংস্কৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক এক–ধরনের উপনিবেশিক আধিপত্যই বহাল রাখে। এটি কেবল ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি অপরাপর সংস্কৃতির বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শনেরই ব্যাপার নয়। এটি অপর সংস্কৃতির উপনিবেশায়ন—যদিও ঘটনা সাপেক্ষে এর তীক্ষ্ণতা ও ঘনত্বে তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। এই সম্পর্কের প্রথম শর্তই হলো, দমিত অধিবাসীদের ভাবনার উপনিবেশায়ন, [যার] ফলে এটি কাজই করে ভাবনার অন্তর্গত হয়ে—যেন ভাবনারই তা নিজস্ব উপাদান।
উপনিবেশায়ন শুরুতে বৈশ্বিক উপনিবেশিক আধিপত্যে অকার্যকর নির্দিষ্ট বিশ্বাস, ভাবাদর্শ, মানসচিত্র ও প্রতীকসমূহের অথবা জ্ঞানকাণ্ডের পদ্ধতিগত দমনের ফলই শুধু ছিলো না, উপনিবেশকেরা একইসঙ্গে উপনিবেশিতদের দখলচ্যুত করেছিলো তাদের জ্ঞানাভিজ্ঞতা [থেকে], বিশেষ করে খনি–শিল্প, কৃষি, প্রকৌশল, উপরন্তু তাদের পণ্য ও শ্রম থেকে। সর্বোপরি, এই দমনের প্রভাব গিয়ে পড়েছে জানা–বোঝার প্রক্রিয়ায় (modes of knowing); জ্ঞানোৎপাদনে; পরিপ্রেক্ষিত, মানসচিত্র ও মানসচিত্র–ব্যবস্থা, প্রতীক ও অর্থোৎপাদনের উপায়ে (modes of signification); বুদ্ধিবৃত্তিক বা ঐক্ষিক (visual), সংহত ও বিষয়কৃত (objectivised) অভিব্যক্তির উৎস, বিন্যাস ও হাতিয়ারে। শাসকগোষ্ঠীর নিজস্ব অভিব্যক্তির বিন্যাস, তাদের বিশ্বাস ও মানসচিত্রসমূহকে অতি–প্রাকৃতিক জ্ঞানপূর্বক আরোপণের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে। এইসকল বিশ্বাস ও মানসচিত্র শাসিতদের সংস্কৃতিগত উৎপাদনকেই কেবল ব্যাহত করেনি, একইসঙ্গে এগুলো ছিলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণেরও অতি কার্যকর হাতিয়ার, বিশেষ করে প্রত্যক্ষ দমনকার্যক্রম যখন থমকে [গিয়ে] স্থির ও প্রণালীবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো।
উপনিবেশকেরা অবশ্য জ্ঞান ও তদর্থ উৎপাদনের নিজস্ব বিন্যাস সম্পর্কেও একটি বিভ্রান্তিকর মানসচিত্র আরোপ করেছিলো। প্রথমত, তারা তাদের বিন্যাসটিকে স্থাপন করেছিলো শাসিতদের নাগালের বাইরে। তারপর, তারা তা শিখিয়েছিলো অসম্পূর্ণ ও নির্বাচিত কায়দায়, যাতে শাসিতদের একটি অংশকে তাদের নিজস্ব ক্ষমতা–সংস্থায় কাজে লাগানো যায়। ফলে, ইউরোপীয় সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিলো ক্ষমতায় পৌঁছানোর সিঁড়ি। সর্বোপরি, দমন–পীড়নের বাইরে প্রলোভনই [যেখানে] সকল ক্ষমতার অব্যর্থ হাতিয়ার। সাংস্কৃতিকভাবে ইউরোপীয় হয়ে ওঠা [তাই] আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। এটি ছিলো উপনিবেশিক ক্ষমতায় অংশগ্রহণের—কিন্তু তা বিলোপের কাজেও এটি খাটতে পারতো—এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের অনুরূপ বস্তুগত সুবিধা ও ক্ষমতা লাভের উপায়স্বরপ: সংক্ষেপে বললে, প্রকৃতিকে পদস্থ করতে—‘উন্নয়নের’ দোহাই। ইউরোপীয় সংস্কৃতি হয়ে উঠেছিলো সংস্কৃতির বৈশ্বিক আদর্শ। অ–ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে সেই মানসপ্রতিমা এখন কদাচিৎ টিকে আছে, সর্বোপরি, এই মতাদর্শিক প্রভাবের বাইরে নিজেকে যা পুনরুৎপাদনে সক্ষম।
সময় ও ঘটনাভেদে সাংস্কৃতিক এই উপনিবেশিকতার রকম ও ফলাফলে যথেষ্ট ফারাক বিদ্যমান। লাতিন আমেরিকায় [যেমন] বিদ্যমান সংস্কৃতির দমন ও মানসপ্রতিমার উপনিবেশায়ন চরিতার্থ হয়েছিলো বিপুল ও ভয়াবহ মাত্রায় স্থানীয়দেরকে নিধনের দ্বারা, প্রধানত ব্যয়সাধ্য শ্রমশক্তি (disposable labor) হিসেবে তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে, তার উপর প্রভুত্ব স্থাপনের সহিংসতা তো ছিলোই, আর ছিলো ইউরোপীয়দের দ্বারা বাহিত রোগসমূহ। আজটেক–মায়া–ক্যারিবীয় ও টোয়ানটেনসুইউ (অথবা ইনকা) (Tawantinsuyana) অঞ্চলে ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন অধিবাসী নিধনের শিকার হয়েছে। এই ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রাগত ভয়াবহতা ছিলো এতোটাই–যে এটি কেবল জনসংখ্যাগত দুর্যোগই ঘটায়নি, সমাজ ও সংস্কৃতিকেও তা সমূলে বিনাশ করেছে। সাংস্কৃতিক অবদমন ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ সামষ্টিকভাবে আমেরিকার এক–সময়কার উন্নত সংস্কৃতিকে নিরক্ষর, বাচনিকতায় (orality) আবদ্ধ চাষীদের এক উপসংস্কৃতিতে নামিয়ে আনে; তাকে বঞ্চিত করা হয় নিজস্ব বিন্যাসে সংহত, বিষয়কৃত, তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সুনম্য (plastic) বা ঐক্ষিক অভিব্যক্তি থেকে। অতঃপর, উত্তরজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সুনম্য অথবা ঐক্ষিক কোনো সংহত ও বিষয়কৃত অভিব্যক্তির স্বতন্ত্র উপায় আর থাকবে না, তবে শাসকদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে, অভিব্যক্তির অন্য চাহিদাসমূহ সঞ্চারিত করতে ক্ষেত্রবিশেষে এমনকি তাদের যদি ধ্বংসও করতে হয়। লাতিন আমেরিকা, নিঃসন্দেহে, ইউরোপ কর্তৃক সাংস্কৃতিক উপনিবেশায়নের এক চূড়ান্ত নজির।
এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চ সংস্কৃতিকে এমন তীব্র ও গভীরভাবে ধ্বংস করা যেত না। তথাপি তাদের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিলো অধীনতার সম্পর্কসূত্রে; [ফলে] ইউরোপীয় দৃষ্টিতে তো বটেই, স্থানীয় ধারকদের চোখেও তা অভিন্ন ছিলো। পশ্চিমা বা ইউরোপীয় সংস্কৃতি আপনকার অগ্রবর্তী সমাজের রাজনীতিক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার মাধ্যমে চিন্তাকাঠামোগত নিজস্ব নকশা ও মুখ্য জ্ঞানমূলক উপাদানগুলোকে সকল ধরনের সংস্কৃতি বিকাশেরই নিয়মরূপে আরোপ করেছিলো, বিশেষত—বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল তৎপরতার ক্ষেত্রে। এই সম্পর্ক পরিণামে সেই ধরনেরই সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনের শর্ত হয়ে উঠেছিলো যা সর্বাত্মক অথবা আংশিকভাবে ইউরোপীয়করণের দিকে ধাবিত হবে।
আফ্রিকায় সংস্কৃতির বিনাশ নিশ্চিতভাবেই এশিয়ার তুলনায় অনেক বেশি গভীর ছিলো, তারপরও তা ছিলো আমেরিকার চেয়ে কম। ইউরোপীয়রা সেখানে কেবল অভিব্যক্তির বিন্যাসেই নয়, বিশেষভাবে বিষয়করণ ও ঐক্ষিক রূপায়ণেরও সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধনে সফল হয়েছিলো। ইউরোপীয়রা যেটা করেছিলো, বৈশ্বিক সংস্কৃতির ক্রমে ইউরোপীয় বিন্যাসের আধিপত্যের দ্বারা আফ্রিকাকে বঞ্চিত করেছিলো তার উত্তরাধিকার ও স্বীকৃতি থেকে। প্রথমটি [আফ্রিকার সংস্কৃতি] সেখানে ‘অদ্ভুত’ বর্গে সীমায়িত হয়েছিলো। যেমনটা, নিঃসন্দেহে, স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমা বা ইউরোপীয় ঘরানার আফ্রিকার শিল্পীদের শিল্পকর্মে আফ্রিকার উৎপন্নের সুনম্য অভিব্যক্তিকে প্রেষণা, সূচনা–বিন্দু ও প্রেরণার উৎসরূপে ব্যবহারের মধ্যে; তা কিন্তু আফ্রিকার শিল্পের নিজস্ব অভিব্যক্তি, ইউরোপীয় মানদণ্ডেরই সমমর্যাদাপূর্ণ আরেকটি মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হয়নি। এবং এটিই নির্ভুলভাবে উপনিবেশিক দৃষ্টিটাকে চিহ্নিত করে দেয়।
উপনিবেশিকতা, [সেই] তখন থেকেই, এমনকি আজকের পৃথিবীতেও প্রভাববিস্তারের সবচেয়ে সাধারণ কায়দা; উপনিবেশবাদ একদা স্পষ্ট রাজনীতিক নকশাক্রম হিসেবে বিধ্বস্ত হয়েছিলো—নিঃসন্দেহে, শোষণের উপায় ও জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের ধরন হিসেবে নয়; [অর্থাৎ] এর শর্তসমূহ ক্ষয়ে যায়নি। [ফলে] ৫০০ বছর ধরে জারি থাকা তাদের প্রধান নির্মাণ কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়নি। [তবে] আগেকার সময়ের উপনিবেশিক সম্পর্ক সম্ভবত একই ফলাফল বয়ে আনতো না, এবং, সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, সেগুলো কোনো বৈশ্বিক শক্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ ছিলো না।
‘জনগোষ্ঠী’ ও ক্ষমতার উপনিবেশিকতা
উপনিবেশক ও উপনিবেশিত এই দুই শ্রেণিতে সমাজকে বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে ‘জনগোষ্ঠী’কে মৌল বর্গরূপে গ্রহণ করা এবং আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে ক্ষমতার উপনিবেশিকতার বাস্তবায়ন একইসঙ্গে ঘটেছিলো। উপনিবেশবাদের অন্যান্য অতীত অভিজ্ঞতার অননুরূপ, প্রবলের শ্রেষ্ঠত্ব আর দুর্বলের অধঃস্তনতার পুরোনো ধারণা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদে জৈবিকভাবে ও গঠনগত উপায়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও অধঃস্তনতার সম্পর্কে পরিবৃত্তি লাভ করেছে।*
সংশ্লিষ্ট শতকগুলোতে নয়া পৃথিবীর ক্ষমতার এই ইউরোকেন্দ্রীকরণ–প্রক্রিয়া দুনিয়ার জনসংখ্যা ও তাদের সমাজকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সূচিত করার ক্ষেত্রে ‘বর্ণবাদী’ মানদণ্ড আরোপণের পথ করে দেয়। ফলে, সাধারণ সব ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে ‘জনগোষ্ঠী’গত বাহ্যিক রূপকেই আমলে নিয়ে, গোটা দুনিয়া জুড়ে গড়ে ওঠে মানুষের নতুন নতুন পরিচয় : ‘সাদা’, ‘ভারতীয়’, ‘নিগ্রো’, ‘হলদে’, ‘হলদে–বাদামি’। তারপর এই ফোঁড়েই গ্রথিত হয় ভূগোলকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পরিচয় : ইউরোপীয়, আমেরিকান, এশীয়, আফ্রিকান এবং আরও পরে ওশেনীয়। পৃথিবীব্যাপী ইউরোপীয় উপনিবেশিক আধিপত্যের কালে—পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায়—চাকরিজীবী, স্বাধীন চাষা, স্বয়ংসম্পূর্ণ বণিক, গোলাম ও ভূমিদাসদের কর্মপরিসর এই ‘বর্ণবাদী’ রেখাতেই চিত্রিত হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী সমাজ ও রাষ্ট্রের জাতীয়করণ, জাতিরাষ্ট্র–সংগঠন, নাগরিকত্ব, গণতন্ত্র ও অপরাপর বিষয়াবলির গঠন–প্রক্রিয়ার সঙ্গেও সর্বতোভাবে সংসৃষ্ট। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সংগ্রামগুলো বৈশ্বিক–পুঁজিবাদী–ব্যবস্থায় নির্ধারিত কর্মপরিসরের এই ধরনে ক্রমশ পরিবর্তন আনতে শুরু করেছিলো, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ–পরবর্তী সময়ে, পুঁজিবাদের নিজস্ব পরিবর্তিত চাহিদাও এক্ষেত্রে দায়ী। কিন্তু কর্মপরিসর নির্ধারণের আদতে সমাপ্তি ঘটেনি—যেহেতু ইউরোকেন্দ্রিক ক্ষমতার উপনিবেশিকতা ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছে যে ইউরোকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদের চেয়েও তা দীর্ঘস্থায়ী। এটা ধরতে না পারলে, লাতিন আমেরিকা ও সংশ্লিষ্ট অপরাপর ভূখণ্ডে পুঁজির ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা মুশকিল।**
সুতরাং, ইউরোকেন্দ্রিক বিশ্বক্ষমতার ছত্রছায়ায় ক্ষমতার উপনিবেশিকতার ভিত্তি ‘জনগোষ্ঠী’র মানদণ্ডে গোটা দুনিয়ার জনসংখ্যার বিন্যস্তকরণের উপরে প্রোথিত। কিন্তু ক্ষমতার উপনিবেশিকতা আদৌ সামাজিক সম্পর্কের ‘বর্ণবাদী’ সমস্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয়। এটি ক্ষমতার উপনিবেশিকতার ভিত্তিমূল হয়ে ওঠার জন্য ইউরোকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী উপনিবেশিক/ আধুনিক বিশ্বক্ষমতার বুনিয়াদি দৃষ্টান্তগুলোকে পরিব্যপ্ত ও সমন্বিত করেছিলো।
ইউরোকেন্দ্রিকতা, সাংস্কৃতিক উপনিবেশিকতা ও আধুনিকতা/ যৌক্তিকতা
ইউরোপীয় উপনিবেশিক আধিপত্য সুদৃঢ় হওয়ার অনুরূপ কালপর্বেই গড়ে ওঠছিলো ইউরোপীয় আধুনিকতা/ যৌক্তিকতার সাংস্কৃতিক সৌধ। আন্তঃবিষয়ী জগৎ সমগ্র ইউরোকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী উপনিবেশিক শক্তি দ্বারা নির্মিত যা ইউরোপীয়দের দ্বারাই বিস্তৃত ও সংহত হয়েছে আর তা প্রতিষ্ঠাও পেয়েছে বিশেষ ইউরোপীয় ফসল হিসেবে ও জ্ঞানের সর্বজনীন চিন্তাকাঠামো রূপে এবং মানবিকতা ও বাদবাকি দুনিয়ার মধ্যেকার সম্পর্ক আকারে। আধুনিকতা/ যৌক্তিকতার ব্যাখ্যার সঙ্গে উপনিবেশিকতার সঙ্গম কোনোভাবেই আকস্মিক ছিলো না, যেমনটা যৌক্তিক জ্ঞানের ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামো যেখানে আলোচিত হয়েছে সেই ব্যাখ্যার মধ্যে স্পষ্টই দেখানো হয়েছে। এছাড়া, নগরের উত্থান ও সামাজিক সম্পর্কের পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিন্তাকাঠামো নির্মাণেও ক্ষমতার উপনিবেশিকতার চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ রয়েছে, উপনিবেশবাদ ও উপনিবেশিকতার বাইরে পালাক্রমে যাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করাই সম্ভব হয়নি বিশেষভাবে তা হয়নি লাতিন আমেরিকা ক্ষেত্রে।
ইউরোপীয় আধুনিকতা/ যৌক্তিকতার চিন্তাকাঠামো নির্মাণে উপনিবেশিকতার নিশ্চায়ক ভার সেই সাংস্কৃতিক সৌধের অন্তর্গত সংকটের মধ্যেই স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। সৌধটির মৌলিক কিছু সমস্যার বিশ্লেষণ তার সংকট বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।
জ্ঞানোৎপাদন প্রসঙ্গে
যৌক্তিক জ্ঞানের ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোর চলতি সংকট দিয়েই শুরু হোক, যার মৌলিক পূর্বানুমানটাই প্রশ্নবিদ্ধ: অর্থাৎ, জ্ঞানকে বিষয়ী–বিষয় সম্পর্কের উৎপাদন মনে করা। জ্ঞান যা সূচিত করে তার বৈধকরণের সমস্যা ছাড়াও, সেই পূর্বানুমান আরও কিছু নতুন সংকটের জন্ম দেয় তা বরং এখানে বিশ্লেষণ করাই শ্রেয়।
প্রথমত, সেই পূর্বানুমানে ‘বিষয়ী’ বর্গটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, কারণ নিজেই তা নিজের মধ্যে ও নিজের জন্য, বয়ানের নিজস্ব পরিসীমায় এবং জাহির করার সাধ্যের ভেতর নিজেকে সংগঠিত করে তোলে। কার্তেসীয় ‘Cogito ergo sum’ (আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি) হুবহু এই অর্থটিই দেয়। দ্বিতীয়ত, ‘বিষয়’ কেবল ‘বিষয়ী’/ ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্দেশক একটি বর্গই নয়, পরেরটি থেকে বৈশিষ্ট্যগতভাবেও তা পৃথক। তৃতীয়ত, ‘বিষয়’ ও তার সত্তা অভিন্ন, কেননা তা পরিগঠিত হয়েছে ‘সম্পত্তি’ দ্বারা যা তার পরিচয় নির্মাণ করে ও তাকে সংজ্ঞায়িত করে, অর্থাৎ, তারা তাকে সীমায়িত করে এবং একই সময়ে স্থাপন করে অপরাপর ‘বিষয়াবলির’ সম্পর্কের মধ্যে।
এই চিন্তাকাঠামোর মধ্যে, প্রথমত, যা প্রশ্নের সম্মুখীন, ব্যক্তি ও ‘বিষয়ী’র ব্যক্তিতান্ত্রিক চরিত্র, যা আন্তঃবিষয়ীতা ও সামাজিক অখণ্ডতাকে সকল প্রকার জ্ঞানের উৎপাদনক্ষেত্র হিসেবে অস্বীকার করার মাধ্যমে যেকোনো অর্ধসত্যের মতো সমস্যাকে আরও ঘোলাটে করে তোলে। দ্বিতীয়ত, [সেখানকার] ‘বিষয়’–এর ধারণা হাল আমলের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, যেই মতে ‘সম্পত্তি’ হলো প্রদত্ত ক্ষেত্রে বিরাজমান কোনো সম্পর্কের উপায় ও সময় নির্দেশক। ফলে, সম্পর্কের এই পরিধির বাইরে সত্তাগতভাবে অহ্রাসযোগ্য মৌলিকতার পরিচয়গত কোনো ধারণা গড়ে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ নেই। তৃতীয়ত, প্রকৃতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ‘বিষয়ী’ ও ‘বিষয়’–এর মধ্যেকার সম্পর্কের বিশ্লিষ্টতা, পার্থক্যসমূহের কেবল যথেচ্ছা অতিকথনই নয়, আধুনিক অনুসন্ধানগুলো যেহেতু জগতে বিরাজমান আরও গভীরতর কোনো যোগাযোগের কাঠামোকেই বরং নির্দেশ করে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও চূড়ান্ত কথা হলো, এই ধরনের জ্ঞানগত অভিপ্রায়ে প্রোথিত থাকে নতুন এক কট্টর দ্বৈতবাদ : ঐশী হেতু ও প্রকৃতি। ‘বিষয়ী’ সেই ‘হেতু’র ধারক ও বাহক, যেখানে ‘বিষয়’ কেবল তা থেকে বিশ্লিষ্টই নয়, বৈশিষ্ট্যগতভাবেও তা স্বতন্ত্র। বাস্তবিকপক্ষে, এটি হলো ‘প্রকৃতি’।
‘বিষয়ী’র ধারণা দিয়ে অবশ্যই কেউ ইউরোপের চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক কাঠামোয় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি, রুদ্ধ ব্যক্তির মুক্ত বিকাশের কোনো উপাদান বা মুহূর্তকে বুঝতেই পারে। দুইয়ের মধ্যে এই পরে উল্লেখিতরা জীবনব্যাপী ব্যক্তির এই একক অধিষ্ঠান ও সামাজিক ভূমিকার নিন্দা করেন, যেমনটা ঘটে থাকে ঠিক সেই ধরনের সমাজে যেখানে কর্তৃত্বক্রম ত্রাস, ভাবাদর্শ ও সাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিমাপুঞ্জের দ্বারা কট্টরভাবে প্রতিষ্ঠিত। এটি ছিলো প্রাগাধুনিক ইউরোপীয় সমাজ/ সংস্কৃতির ঘটনা। সেই স্বাধীনতা ছিলো পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক ও নাগরিক জীবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই। কিন্তু, আরেক দিক থেকে দেখলে, জ্ঞানচর্চার বর্তমান ক্ষেত্রে সেই প্রস্তাবনা আজ অচল। একক সেই বিশ্লিষ্ট বিষয়ীতা বাস্তব, কিন্তু মোটেও তা স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নয়, ফলে এটি নিজ অস্তিত্বের মুখোমুখি বা স্বয়ং অস্তিত্বশীল নয়। এটি অস্তিত্বশীল সামাজিক সম্পর্কের আন্তঃবিষয়ীতা বা আন্তঃবিষয়ী মাত্রার পৃথক অংশ হিসেবে—বিচ্ছিন্ন রূপে নয়। প্রতিটি একক বয়ান, অথবা অনুচিন্তন আন্তঃবিষয়ী কাঠামোকেই নির্দেশ করে। এটি নিজের মধ্যে নিজেরই মুখোমুখি সংগঠিত হয়। জ্ঞান এই বিবেচনায় কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে এক–ধরনের আন্তঃবিষয়ী সম্পর্ক, বিচ্ছিন্ন বিষয়ীর সঙ্গে সেই কিছু একটার সম্পর্ক মাত্র নয়।
সম্ভবত সম্পত্তির অনুরূপ উপায়ে জ্ঞানকে—একক ব্যক্তির সঙ্গে আর কিছুর সম্পর্ক আকারে—বিবেচনা করাটা আকস্মিক নয়। আধুনিক সমাজ বিকাশের মুহূর্তেও অনুরূপ মানসিক নকশা এই দুই ধারণাকে বলবৎ রেখেছিলো। ফলে, সম্পত্তিও, জ্ঞানের অনুরূপ, কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে তৎপর লোকেদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক [কিংবা] একক ব্যক্তির সঙ্গে আর কিছুর সম্পর্কমাত্র নয়। এইসব প্রপঞ্চ পার্থক্য নির্দেশ করে যে সম্পত্তি–সম্পর্ক জারি থাকে বস্তুগত একইসঙ্গে আন্তঃবিষয়ী কায়দায়; অপরপক্ষে, জ্ঞান হাজির থাকে কেবলই আন্তঃবিষয়ী সম্পর্করূপে।
ফলে, যে–কেউ যৌক্তিকতার ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোর বিস্তৃতিকালের সঙ্গে ব্যক্তিবাদ/ দ্বৈতবাদ এবং ইউরোপীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বসমূহের সংশ্লিষ্টতা দেখাতেই পারেন। কিন্তু সেই ব্যক্তিবাদ/ দ্বৈতবাদে আরও একটি অনুষঙ্গ আছে, ইউরোপীয় অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষিতে যা অপ্রাসঙ্গিক নয়: ‘অপর’ একদম গরহাজির; অথবা হাজির থাকলেও তা কেবলই ‘বিষয়কৃত’ উপায়ে।
সাধারণত ‘অপর’–এর এই কট্টর অনুপস্থিতি, সামাজিক অস্তিত্বের অণুপ্রতিমাকেই কেবল প্রামাণ্যরূপে পেশ করে না, এর মানে, সামাজিক অখণ্ডতার ধারণাকেও তা অস্বীকার করে। ইউরোপীয় উপনিবেশিক অনুশীলনে যেমনটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে এই চিন্তাকাঠামোয় ইউরোপীয় পটভূমির বাইরের যেকোনো অপর ‘বিষয়ী’র উল্লেখকে একদম গায়েব করে দেওয়া সম্ভব, অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে উপনিবেশিক ক্রমকে অদৃশ্য রাখতে ঠিক একই সময়ে উপনিবেশ কবলিত বাদবাকি দুনিয়ার সাপেক্ষে ইউরোপ গড়ে তুলছিলো তার নিজস্ব আত্মপরিচয়। ‘পশ্চিম’ অথবা ‘ইউরোপ’ নামক ধারণার আবির্ভাব মূলত অন্যান্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাসমূহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক—অপরাপর সংস্কৃতির মধ্যেকার জারি থাকা পার্থক্যসমূহের সাপেক্ষে পরিচিতির প্রতিপাদন। কিন্তু, সেই ‘ইউরোপীয়’ বা ‘পশ্চিমা’ বোঝাপড়ায়, সর্বোপরি, এই বৈচিত্র্যসমূহ প্রাথমিকভাবে কর্তৃত্বক্রমানুযায়ী পূর্ণমাত্রায় অসমতা হিসেবে প্রতিপাদিত হয়েছে। এবং এই অসমতাগুলোকে জ্ঞান করা হয়েছে প্রকৃতি প্রদত্ত বলে : ইউরোপীয় সংস্কৃতিই কেবল যুক্তিসিদ্ধ, এটি ‘বিষয়ী’কে ধারণে সক্ষম—বাদবাকি আর যা আছে সেগুলো যুক্তিসিদ্ধ নয়, ‘বিষয়ী’ হতে তারা অপারগ বা তা ধারণেও অক্ষম। ফলে শেষমেষ দাঁড়ালো এই, অপরাপর সংস্কৃতিগুলো এই কারণেই পৃথক যে তারা অসম, আসলে অধঃস্তন, এবং তা প্রকৃতিগভাবেই। তারা কেবল হতে পারে জ্ঞান বা কর্তাগিরি ফলানোর ‘বিষয়’ মাত্র। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নির্ধারিত হয়েছে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও অপরাপর সংস্কৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক এবং তা সংরক্ষিতও হয়েছে ‘বিষয়ী’ ও ‘বিষয়’–এর মধ্যেকার সম্পর্করূপে। ফলে, যোগাযোগের প্রতিটি সম্পর্ককে, সংস্কৃতিসমূহের মধ্যেকার জ্ঞান ও জ্ঞানোৎপাদনের যে উপায়সমূহ রয়েছে তাদের পারস্পরিক বিনিময়কে এটি প্রতিহত করেছে, যেহেতু চিন্তাকাঠামোটিই প্রোথিত করে দেয় ‘বিষয়ী’ ও ‘বিষয়’–এর মধ্যে কেবলই এক বিশ্লিষ্টতার সম্পর্ক। এই ধরনের মানসিকতা চর্চাকারে জারি আছে ৫০০ বছর ধরে, যা কেবল ইউরোপ ও বাদবাকি দুনিয়ার উপনিবেশিক সম্পর্কের ফসলরূপেই সম্ভবপর ছিলো। অন্যভাবে বললে, যৌক্তিক জ্ঞানের ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামো কেবল এই পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, বাদবাকি দুনিয়ার উপর ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসন–সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাকাঠামোর অংশ হিসেবেও বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিপাদন করা অর্থে, এই চিন্তাকাঠামোটিই মেলে ধরেছিলো সেই ক্ষমতাকাঠামোর উপনিবেশিকতা।
ইতোমধ্যেই এসব ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ব থেকে; নির্দিষ্ট কিছু বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ, যেমন নৃতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞান, ‘পশ্চিমা’ সংস্কৃতি ও অপরাপর সংস্কৃতির মধ্যে সর্বদা সেই ধরনের ‘বিষয়ী–বিষয়’ সম্পর্কই নির্দেশ করে আসছে। অপরাপর সংস্কৃতিসমূহ [যেন] সংজ্ঞানুসারেই অধ্যয়নের ‘বিষয়’। সশ্লেষ ব্যঙ্গানুকরণ ব্যতীত (‘Nacirema–দের আচারানুষ্ঠান’—‘American’-এর শব্দখেল—এর আদর্শ নমুনা) ‘পশ্চিমা’ সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে এই ধরনের অধ্যয়ন কার্যত অনস্তিত্বশীল।
জ্ঞানে সমগ্রতার প্রসঙ্গ
কার্তেসীয় চিন্তাকাঠামোয় গরহাজির থাকা সত্তে¡ও, বিশেষ করে সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কের বেলায়, সমগ্রতার ধারণার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনীয়তা ইউরোপীয় আলোচনায় হাজির ছিলো; শুরুর দিকে আইবেরীয় দেশগুলোতে এবং গির্জা ও রাজশক্তির ক্ষমতা সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টায় এবং কিছুটা পরে ফ্রান্সে (আঠারো শতকে), তারও পরে সমাজ পর্যালোচনায় বা বিকল্প সমাজের প্রস্তাবনায় ব্যবহৃত চাবি অনুষঙ্গ হিসেবে। সর্বোপরি, সন্ত সিমোঁর সময় থেকেই, সমাজ–রূপান্তরের বৈপ্লবিক প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অখণ্ডতার ধারণাও বিস্তৃতি লাভ করেছিলো, সামাজিক অস্তিত্বের ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে পরে যা অভিজ্ঞতাবাদী ও বিদ্যমান সমাজ এবং রাজনীতিক কাঠামোর অনুরক্তদের মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বিশ শতকে, সমগ্রতা একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক তদন্তে সচরাচর অবলম্বিত একটি বর্গ হয়ে ওঠে—বিশেষত যেগুলোর কারবার সমাজ নিয়ে।
ইউরোপীয়–পশ্চিমা যৌক্তিকতা/ আধুনিকতা কেবল গির্জা ও ধর্মের সঙ্গে বিবাদমূলক সংলাপ দ্বারাই নয়, গড়ে উঠেছে একদিকে, পুঁজিবাদী এবং নাগরিক সামাজিক সম্পর্ক ও জাতি–রাষ্ট্রসমূহ; অন্যদিকে, বাদবাকি দুনিয়ার উপনিবেশায়ন মারফত ক্ষমতাকে নতুন কাঠামোয় সংস্থাপন করার মধ্য দিয়ে। এটি সম্ভবত, পরিস্থিতি থেকে বিযুক্ত ছিলো না যে সামাজিক সমগ্রতার ধারণাটি বিকশিত হয়েছিলো একটি অবয়ববাদী মানসচিত্রানুসারে, যা বাস্তবতার একটি সীমিত আদলকে গ্রহণে প্ররোচিত করেছিলো।
প্রকৃতপক্ষে, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা সামাজিক সমগ্রতা, অর্থাৎ, সমাজ–এর ধারণার উদ্বোধন ও তাকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে স্পষ্টত সহায়ক ছিলো। কিন্তু আরও দুটি অনুরূপ ধারণা নির্মাণেও এটি সহায়ক ছিলো : এক, প্রতিটি সদস্যের সক্রিয় সম্পর্কের কাঠামো হিসেবে সমাজ, এবং যার–ফলে তা [সমাজ] যুক্ত ছিলো একক একটি যুক্তিকাঠামোর সক্রিয়তার সঙ্গে, সুতরাং, [দাঁড়ালো] এক নিপাট সমগ্রতা। পরবর্তীতে পদ্ধতিগত সমগ্রতার ধারণাটিকে এটি ঠেলে দেয় কাঠামোবদ্ধ–ক্রিয়াবাদে। দ্বিতীয় ধারণাটি ছিলো, আঙ্গিক কাঠামোরূপে সমাজ, যেখানে প্রতিটি অঙ্গ আগের নিয়মেই কর্র্তৃত্বক্রমানুযায়ী পরস্পর সম্পর্কিত, আমাদের মনে প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে ঠিক যে–ধরনের চিত্র আছে, বিশেষভাবে বলা যায় মানবদেহের কথা। যেখানে একটি অংশ (মস্তিষ্ক) সমগ্র দেহটাকেই নিয়ন্ত্রণ করে—অস্তিত্বের স্বার্থে যদিও এটি বাকিদের বর্জন করায় অপারগ—বাদবাকি (বিশেষত হাত ও পা) অংশ অঙ্গসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী অংশের প্রতি আনুগত্য বজায় না–রেখে টিকতেই পারে না।
উদ্যোক্তা–শ্রমিক সম্পর্ক ও শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে জড়িত এটি একটি মনগড়া চিত্র, রোমান প্রজাতন্ত্রের শুরুর দিককার মেনেনিয়াস আগরিপা কিংবদন্তি বক্তৃতাকেই যা প্রলম্বিত করে চলেছে, যা [প্রদান করা হয়ে]ছিলো ইতিহাসের প্রথম হরতালকারীদের নিরত করার উদ্দেশ্যে [যে] : মালিকরা হলো মস্তিষ্কস্বরূপ এবং শ্রমিকরা তার সহায়াঙ্গ, যা দেহের মতো বাদবাকি অঙ্গসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজ গঠন করে। মস্তিষ্ক ব্যতিরেকে যেমন সহায়াঙ্গসমূহের কোনো সার্থকতা থাকবে না, তেমনি বাদবাকি অঙ্গাদির সহায়তা ছাড়াও মস্তিষ্ক অক্ষম। দেহকে সক্রিয় ও বলবান রাখার জন্য উভয়ই সমানভাবে অপরিহার্য অন্যথায় না–মস্তিষ্ক না–বাদবাকি প্রত্যঙ্গ কোনোটাই কার্যকর থাকবে না। কাউটস্কির যে প্রস্তাবটিকে লেনিন আত্মস্থ করেছিলেন, তা এই চিত্রেরই রকমফের মাত্র, প্রলেতারিয়েতরা যেখানে আপনা থেকে নিজেদের শ্রেণি–চেতনার বিকাশ ঘটানোয় অক্ষম এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীশ্রেণি বা পেটি বুর্জোয়া শ্রেণিই হলো সেই শ্রেণি যাদেরকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তাদেরকে [প্রলেতারিয়েত] তা শেখানোর। [ফলে] রাশিয়ার জনতোষকদের (জনগণের যারা বন্ধু) সঙ্গে বাহাসে ইতোমধ্যে যে মতটি লেনিন স্পষ্টভাবে সমর্থন করেছেন যে সমাজ সমগ্র এক দেহের মতো—তা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। লাতিন আমেরিকায় এই চিত্রকল্প পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাইমে পাস সামোরা, সাংবাদিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, বলিভিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে শ্রমিকদের ও পার্টির সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক নির্দেশ করলেন [এই বলে] : পার্টি হলো গিয়ে মাথা, আর ইউনিয়নসমূহ তার পা। ধারণাটি অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও তাদের জনপ্রিয় ভিত্তিগুলোকে প্রতিনিয়তই প্রভাবিত করে চলেছে।
সামাজিক সমগ্রতার এই অবয়ববাদী ধারণা, সমাজ সম্পর্কে, বিষয়ী–বিষয় সম্পর্কের হিসেবে জ্ঞানের সাধারণ চিন্তাকাঠামোর এমনকি তার কোনো রূপভেদের সঙ্গেও সামঞ্জস্যহীন নয়। ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তব–অবলোকনের ক্ষেত্রে একে তারা অপরের বিকল্প, কিন্তু তারা রয়ে যায় একই চিন্তাকাঠামোতে। যাইহোক, উনিশ শতকে ও বিশ শতকের একটা বড়ো সময় ধরে, সমাজ পর্যালোচনা ও তার রূপান্তরের প্রস্তাবসমূহ এই অবয়বী ভাবনা দ্বারা ঠেকনা পেতে পারতো, কারণ পরেরটি ক্ষমতার বিদ্যমানতাকে জাহির করে সমাজের সমন্বয়ক হিসেবে। এভাবেই এটি সমাজে ক্ষমতার প্রসঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও সেই সম্পর্কিত তর্ক জারি রাখতে ভূমিকা পালন করে।
অন্যদিকে, সেইসব অবয়ববাদী ধারণাসমূহ উপনিবেশবাদের দ্বারা সজ্জিত বিন্যাস সমজাতীয় না–হওয়া সত্তে¡ও ঐতিহাসিকভাবে সমজাতীয় সমগ্রতার পূর্বানুমানকে আরোপ করে। সুতরাং, উপনিবেশিত অংশ সেই সমগ্রতার অভ্যন্তরীণ, নিম্নদেশস্থ, কিছু নয়। এটা সুবিদিত যে, আলোকসম্পাত কালের ইউরোপে ‘মানবতা’ ও ‘সমাজ’–এর মতো বর্গসমূহ অ–ইউরোপীয় মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো না, অথবা তা ছিলো কেবলই আনুষ্ঠানিকতায়, নির্দিষ্ট অর্থে এই–ধরনের অভিজ্ঞার আদতে কোনো প্রায়োগিক সার্থকতা ছিলো না। যে–কোনো ক্ষেত্রেই, বাস্তবতার অবয়বী চিত্রানুসারে, সমগ্র অবয়বের মস্তিষ্কস্বরূপ ছিলো শাসনকারী কর্তৃপক্ষ—ইউরোপ, আর পৃথিবীর প্রত্যেকটি উপনিবেশিত ভূখণ্ডে—ইউরোপীয়রা। অতি পরিচিত ফাচুকি মন্তব্যটি যে উপনিবেশিত লোকেরা ছিলো ‘সাদা মানুষদের বোঝা’, সেই চিত্রকল্পের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত।
শেষাবধি, সমগ্রতার ধারণাটি, এইভাবে কর্তৃত্বক্রমানুযায়ী সাজানো বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার ব্যবহারিক সম্পর্কের এক অন্তরঙ্গ কাঠামো হিসেবে সমাজের চিত্রকল্প নির্মাণ করেছে যা ঐতিহাসিক সমগ্রতার প্রয়োজনে আগেভাগেই অনুমান করে নিয়েছে অদ্বিতীয় এক ঐতিহাসিক যুক্তিবিদ্যা, এবং সমগ্রতার সেই অদ্বিতীয় যুক্তিবিদ্যায় প্রতিটি অংশেরই বশ্যতার শর্তে সংগঠিত হয়েছে এক–ধরনের যৌক্তিকতাও। সমাজকে এটি ঐতিহাসিক যৌক্তিকতার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা বৃহত্তর এক ঐতিহাসিক বিষয়ীরূপে বুঝতে উদ্বুদ্ধ করে, যথারীতি সেটি সমগ্র ও তার অংশগুলোর আচরণ, একইসঙ্গে সময়ের প্রেক্ষিতে তার অভিমুখ ও বিকাশের চূড়ান্ত অবস্থা সম্পর্কিত ভাবীকথনসমূহেরও অনুমোদন দেয়। সমগ্রতার শাসনকারী অংশরূপে, কোনোভাবে, সেই ঐতিহাসিক যুক্তিবিদ্যাই আবির্ভূত হয়, উপনিবেশিত দুনিয়ার সাপেক্ষে—যা মূলত ইউরোপ। অতঃপর এ আর আশ্চর্যজনক নয়, ইতিহাসকে [যে] বোঝা হয়েছিলো আদিম থেকে সভ্য, প্রথাবদ্ধতা থেকে আধুনিকতা; বর্বর থেকে যৌক্তিক; প্রাক–পুঁজিবাদ থেকে পুঁজিবাদ—এইসব বিবর্তনমূলক পরম্পরায়। এবং ইউরোপ নিজেকে বিবেচনা করলো, গোটা প্রজাতির মধ্যে ইতিহাসের সর্বোচ্চ বিকশিত পর্যায় হিসেবে, অপরাপর সমাজ ও সংস্কৃতির ভবিষ্যতের দর্পণরূপে। যাইহোক, যা [আর] বিস্ময় ঠেকাতে পারলো না, তা হলো ইউরোপ উপনিবেশিত সংস্কৃতির প্রায়োগিক সমগ্রতার উপর সেই ‘মরীচিকা’ আরোপণে সফল হয়েছিলো; এবং, এর চেয়েও বড়ো কথা, এই অলীক কল্পনাটিই অনেকের কাছে এখনও সমান আকর্ষণীয়।
জ্ঞানতাত্ত্বিক পুনর্গঠন: বি–উপনিবেশায়ন
সমগ্রতার ধারণাটি সাধারণত ইউরোপেই এখন প্রত্যাখ্যাত ও প্রশ্নের সম্মুখীন, শুধুমাত্র বারোমাইস্যা অভিজ্ঞতাবাদীদের দ্বারাই নয়, গোটা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মহলের কাছেও নিজেদের যারা উত্তরাধুনিক বলে পরিচয় দেয়। ইউরোপে সমগ্রতার ধারণাটি আসলে উপনিবেশিকতা/ আধুনিকতারই ফসল। এবং এটি দেখানোও সম্ভব, যেমনটা আমরা উপরে দেখেছি যে, সমগ্রতার ইউরোপীয় ধারণাটি [এক–ধরনের] তাত্ত্বিক সংকোচন ও বৃহত্তর এক ঐতিহাসিক বিষয়ীর অধিবিদ্যার দিকে ঠেলে দেয়। তার উপর, এই–সকল ধারণা অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনীতিক চর্চা ও সমাজের সামগ্রিক যৌক্তিকীকরণের অচেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
যাইহোক, ইউরোপীয় আধুনিকতার পরিসরে যে–সকল ধারণা ও চিত্রকল্পের দ্বারা সমগ্রতার বর্গটি গড়ে উঠেছে তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এর প্রতিটি ধারণাটিকেই বর্জন করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যা করতে হবে, তা বরং বেশ আলাদা রকমের কিছু: জ্ঞানের উৎপাদন, প্রতিফলন ও বিনিময়কে ইউরোপীয় আধুনিকতা/ যৌক্তিকতার চোরাটান থেকে মুক্ত করা।
‘পশ্চিম’–এর বাইরে, কার্যত অধিকাংশ পরিচিত সংস্কৃতিরই—প্রতিটি বিশ্ববীক্ষা, প্রতিটি চিত্রকল্প—জ্ঞানের যাবতীয় পদ্ধতিগত উৎপাদন অখণ্ডতার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু সেই সংস্কৃতিসমূহে, জ্ঞানকাণ্ডের অখণ্ডতার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করে নেয় বাস্তবতার সকল ধরনের বিষমজাতীয়তাকে; পরেরটির [অ–পশ্চিমের] অহ্রাসযোগ্য, বৈপরীত্যমূলক চরিত্রকে; [তার] বৈধতাকে; অর্থাৎ, সব–রকমের বাস্তবতার উপাদানসমূহের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের কাম্যতাকে—ফলে, তাদের সামাজিক স্বীকৃতিকেই। সামাজিক অখণ্ডতার ধারণাটি, ফলে, কেবল যে অস্বীকারই করে না তা নয়, প্রতিটি সমাজের ঐতিহাসিক বৈচিত্র ও সমাজের বিষমজাতীয়তার ধারণার উপর তা নির্ভরশীলও বটে। অন্যভাবে বললে, বিচিত্র, ভিন্ন—‘অপর’–এর ধারণাকে তা যে কেবল খারিজই করে না তা নয়—এটি তার জন্য প্রয়োজনীয়ও বটে। সেই ভিন্নতা ‘অপর’–এর অসম প্রকৃতিকে এবং তাই সম্পর্কসমূহের পরম বিশ্লিষ্টতাকে অনিবার্যরূপে সূচিত করে না; না সূচিত করে কর্তৃত্বক্রমের অসমতাকে, না অপরের উপর সামাজিক অধস্তনতাকে। বৈচিত্র্যসমূহই অবশ্যম্ভাবীরূপে আধিপত্যের ভিত্তি নয়। একই সময়ে—এবং সেই কারণেই—ঐতিহাসিক–সাংস্কৃতিক বিষমজাতীয়তা সূচিত করে সম–হাজিরা ও তাদের কোনো একটিকে ঘিরে বিচিত্র–রকম ঐতিহাসিক ‘যুক্তিবিদ্যা’র সংযোজন যা নেতৃস্থানীয় কিন্তু কোনোভাবেই অদ্বিতীয় নয়। [ফলে] এদিক দিয়ে, সরলীকরণের যাবতীয় পথ বন্ধ, একইরকমভাবে বন্ধ আপন যৌক্তিকতা ও ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যবাদে সমর্থ বৃহত্তর এক ঐতিহাসিক বিষয়ীর অধিবিদ্যার পথ—ব্যক্তিবর্গ বা কোনো নির্দিষ্ট দলপুঞ্জ, উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাক শ্রেণি, যার বাহক বা মিশনারি হতে পারে।
যৌক্তিকতা/ আধুনিকতার ইউরোপীয় চিন্তাকাঠামোর সমালোচনা করাটা অত্যাবশ্যকীয়—এমনকি, আশু কর্তব্যও বটে। কিন্তু সমালোচনাটা যদি হয় এর সমস্ত বর্গসমূহের সরল নেতিকরণ, বয়ান থেকে বাস্তবতার অবসান, বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সমগ্রতার ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশুদ্ধ নেতিকরণ, তাহলে তা মুশকিলের ব্যাপার। যৌক্তিকতা/ আধুনিকতা ও উপনিবেশিকতার মধ্যেকার যে সংযোগ তা থেকে নিজেকে মুক্ত করাটা জরুরি, প্রথমত, এবং সুনির্দিষ্টভাবে যাবতীয় ক্ষমতা থেকে—যা মুক্ত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়নি। এটি ক্ষমতার উদ্দেশ্যে, সর্বাগ্রেই উপনিবেশিক ক্ষমতা, যুক্তিসমূহের যান্ত্রিকীকরণ যা গড়ে তুলেছে জ্ঞানের বিকৃত চিন্তাকাঠামো এবং নস্যাৎ করেছে আধুনিকতার মুক্তিদায়ী প্রতিশ্রুতিসমূহকে। সুতরাং, এর বিকল্পটি স্পষ্ট: বৈশ্বিক ক্ষমতার উপনিবেশিকতাকে ধ্বংস করা। অভিজ্ঞতা ও ভাব বিনিময়ের পথকে প্রশস্ত করতে, নয়া আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায়, যৌক্তিকতার আরেক ভিত্তিস্বরূপ, বি–উপনিবেশিকতা হিসেবে, সবার আগে প্রয়োজন জ্ঞানতাত্ত্বিক বি–উপনিবেশায়ন বৈধভাবেই যা দাবি করবে কতিপয় সর্বজনীনতা। নির্দিষ্ট কোনো নৃগোষ্ঠীর বিশেষ বিশ্ববীক্ষাকে সর্বজনীন যৌক্তিকতাস্বরূপ দাবি করার চেয়ে, পরিশেষে, অযৌক্তিক আর কিছুই হতে পারে না, এমনকি এই–ধরনের কোনো নৃগোষ্ঠীকে যদি পশ্চিম–ইউরোপ নামেও ডাকা হয়—কেননা, এটি আসলে প্রাদেশিকতাকেই সর্বজনীনতা রূপে আরোপণের দাবি করা।
উপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্কসমূহের মুক্তি সর্বসাধারণের, এককভাবে অথবা সামষ্টিকভাবে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মধ্যে থেকে, সর্বোপরি, সমাজ ও সংস্কৃতির উৎপাদন, পর্যালোচনা, পরিবর্তন ও বিনিময়ের উপায় বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাকে সূচিত করে। এই–ধরনের মুক্তি—অসমতা, বৈষম্য, শোষণ ও আধিপত্য হিসেবে সুবিন্যস্ত যাবতীয় ক্ষমতা থেকে—সামাজিক মুক্তি প্রক্রিয়ারই অংশ।
[ইংরেজি অনুবাদের] টীকা
মূল স্প্যানিশ ভাষা থেকে সোনিয়া থেরবর্ন কর্তৃক অনূদিত। প্রবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিলো: Globalizations and Modernities. Experiences, Perspectives and Latin America, Stockholm, FRN-Report, 99: 5, 1.
* কিহানোর ‘নরগোষ্ঠী’ সম্পর্কিত ভাবনার উৎস ধরে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। দেখুন কিহানো (১৯৯২)।
** লাতিন আমেরিকার জন্য, দেখুন কিহানো (১৯৯৩)।
[ইংরেজি অনুবাদের] তথ্যসূত্র
Quijano, Anibal (1992) ‘Raza, Etnia y Nacion: Cuestiones Abiertas’, in JoseCarlosMariateguiyEuropa, ed. Roland Forgues, La otracaradelDescubrimiento, Liina, Amauta, Peru.
—(1993) ‘America Latina en Ia Economia Mundial’, in Problemas dcl Desarrollo, Revista del Instituto de Investigaciones de Ia Facultad de Econornja, UNAM, vol. XXIV, no. 95, Mexico.
(বাংলা অনুবাদের) তথ্যসূত্র ও টীকা
১. কিহানোর ‘Colonialidad y Modernidad/ Racionalidad’ প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ১৯৯১ সালে। (https://globalsocialtheory.org/thinkers/quijano-anibal/) । ১৯৯২ সালে এটি প্রকাশিত হয় Perú Indígena (Lima) প্রত্রিকায়। স্প্যানিশ থেকে সোনিয়া থেরবর্ন (Sonia Therborn) ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেন—Coloniality and Modernity/ Rationality শিরোনামে। থেরবর্নের অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিলো ইয়োরান থেরবর্ন (Göran Therborn) সম্পাদিত Globalizations and Modernities. Experiences, Perspectives and Latin America গ্রন্থে। যে বইটি আসলে ১৯৯৮ সালের ২৮ জুন থেকে ১ জুলাই অবধি সংঘটিত বুয়েনস আইরেস সম্মেলনের রিপোর্ট। বুয়েনস আইরেস সম্মেলনটি ছিলো বুদাপেস্ট, ইস্তাম্বুল, ভিলনিয়াস, বেইজিং ও স্টকহোমে অনুষ্ঠিত সম্মেলনগুলোরই পরম্পরা। যাইহোক, সেই মূল অনুবাদটিকে বর্তমান বাংলা অনুবাদের কাজে ব্যবহার করার সুযোগ হয়নি। এখানে অনুসৃত হয়েছে ২০০৭ সালের Cultural Studies পত্রিকার ২১ নম্বর ভলিউমের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অনুবাদটি। পরে অবশ্য সেই একই অনুবাদ ২০১০ সালে ওয়াল্টার দে মিগনোলো ও আরতুরো এসকোবার সম্পাদিত Globalizations and the Decolonial Option গ্রন্থেও ছাপা হয়।
২. https://globalsocialtheory.org/thinkers/quijano-anibal/
৩. https://en.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADbal_Quijano#:~:text=An%C3%ADbal%20Quijano%20(17%20November%201930,decolonial%20studies%20and%20critical%20theory.
৪. https://www.scielo.br/j/cint/a/9BxwGvYxjb6YWswTpddQ9Hm/?format=pdf&lang=en
৫. https://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf
৭. ‘আমরা অনুভবে যাহা পাই, তাহা বুদ্ধি দ্বারা কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। যেসব বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়া পদার্থ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, সেসব প্রকারের দ্বারা বিষয়ের প্রকারভেদ নির্ণীত হয়, একথাও বলিতে পারা যায়। অন্তত বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল পদার্থের প্রকারভেদ নির্দেশের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই শব্দ কান্ট সম্বন্ধাত্মক বৌদ্ধিক প্রকারের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। বুদ্ধিদ্বারা যে সব কতিপয় বিশিষ্ট প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়া পদার্থ আমাদের লৌকিক জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাদিগকে এখানে বৌদ্ধিক প্রকার বলা হইতেছে। এই অর্থে কান্ট ক্যাটিগরি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (রাসবিহারী, ২০১১ : ৪৩)।’ অ্যারিস্টটল যে অর্থে category-শব্দটাকে ব্যবহার করেছেন, কান্ট কিন্তু ঠিক সেই অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেননি—তারপরও দুইয়ের মধ্যে অর্থগত যোগ কিছুটা রয়েছেই (রাসবিহারী, ২০১১ : ৪৩)। ফলে, এই থেকে পশ্চিমা দর্শনশাস্ত্রে ব্যবহৃত পধঃবমড়ৎু–শব্দটির অর্থ আমরা মোটামুটি অনুমান করে নিতে পারি। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ এর অর্থ করেন—‘জাতি প্রকার’। ক্যাটিগরি বোঝাতে ‘বর্গ’ শব্দটি ইদানিং প্রায় প্রচলিত। তাই, ক্যাটিগরি অর্থে ‘বর্গ’ শব্দের প্রতি আমাদের রায় না–থাকা সত্ত্বেও—পারস্পরিক চিন্তাসূত্রে গিঁট লাগানোর স্বার্থে—‘বর্গ’ শব্দটিই এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৮. এই বাক্যে Perú Indígena (Lima) প্রত্রিকায় ১৯৯২ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মূল স্প্যানিশ সংস্করণের সঙ্গে ২০০৭ সালের Cultural Studies পত্রিকায় অনূদিত ইংরেজি প্রবন্ধের অমিল রয়েছে। ‘…while at the same time the colonizers were expropriating from the colonized their knowledge, specially in mining, agriculture, engineering, as well as their products and work.’—এই অংশটুক মূল প্রবন্ধে নেই। অর্থাৎ, উপনিবেশিতদের নিজস্ব জ্ঞানাভিজ্ঞতা, বিশেষ করে খনি–শিল্প, কৃষি, প্রকৌশল, উপরন্তু পণ্য ও শ্রম থেকে দখলচ্যুত করার প্রসঙ্গ সেখানে অনুপস্থিত।
৯. Perú Indígena সংস্করণে পুরো বাক্যটি এই— Era un modo de participar en el poder colonial pero tambien podia servir para destruirlo y, despues, para alcanzar los mismos beneficios materiales y el mismo poder que los europeos; para conquistar la naturaleza. En fin, para el “Desarrollo”। থেরবর্ন এর অনুবাদ করেছেন— It was a way of participating and later to reach the same material benefits and the same power as the Europeans: viz, to conquer nature ─ in short for ‘development’. অর্থাৎ, ‘pero tambien podia servir para destruirlo’ অংশটুকু নেই। ইংরেজিতে যার অর্থ দাঁড়ায়—but it could also be used to destroy it।
১০. বাংলা অনুবাদে বাক্যটাকে যেন জুৎ মতো ধরা গেলো না। থেরবর্নের অনুবাদে ইংরেজিটা এরকম—Henceforth, the survivors would have no other modes of intellectual and plastic or visual formalized and objectivised expressions, but through the cultural patterns of the rulers, even if subverting them in certain cases to transmit other needs of expression.
১১. ‘Race’-এর ধারণা মানুষকে আসলে কতগুলো মানদণ্ডে ভাগ করে দেখাকে সূচিত করে। এর নেপথ্যের সিদ্ধান্তসমূহ হলো : এক—জাতিসমূহ কতিপয় জৈবিক ভিতের প্রতিনিধিত্ব করে, এটা হতে পারে অ্যারিস্টটলীয় নির্যাস বা আধুনিক জিন অর্থে; দুই—এই জৈবিক ভিত জাতিগত পৃথক দলসমূহ গঠন করে, বিষয়টা এমন–যে কোনো একটা জাতির সবাই এবং কেবল সবাই এমন এক–সেট জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা অপরাপর জাতিসমূহের কেউ ধারণ করে না; তিন—প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই জৈবিক ভিত বাহিত হয়ে নির্ণয়কারীকে বংশ বা কুলজি ধরে কারো জাতি চিনে ফেলার সুযোগ করে দেয়; চার—বংশগত তদন্তে অবশ্যই জাতিটির ভৌগোলিক উৎসের নাগাল থাকা চাই, যেমন আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া, অথবা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা; পাঁচ—প্রবাহিত এই জাতিগত জৈবিক ভিত প্রথমত গায়ের রং, চোখের গড়ন, চুলের বাহার, হাড়ের গঠন ইত্যাদি শারীরিক ফেনোটাইপগুলোর [পরিবেশের সঙ্গে জেনোটাইপের মিথস্ক্রিয়ার অঙ্গজ রূপ] মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে, বুদ্ধিমত্তা বা দুষ্কৃতির মতো আচরণগত ফেনোটাইপগুলো দ্বারাও তার প্রকাশ সম্ভব (James and Adam : 2022)। বাংলা ভাষায় ‘জধপব’–এর প্রতিশব্দ অনেক। কিন্তু কোনো শব্দ দিয়েই জুৎ মতো তাকে ধরা যায় না—কেবল পিছলে যায়। বর্তমান অনুবাদেই একে বর্ণ, জাতি, জনগোষ্ঠী ইত্যাদি শব্দে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।
১২. বাংলা একাডেমির ইংরেজি–বাংলা অভিধানে ‘Rationality’ শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে—যুক্তিসম্পন্নতা; যৌক্তিকতা। তবে এই অনুবাদে ‘Rationality’-র বদলে ‘যৌক্তিকতা’ বসিয়ে দিলেই কিন্তু কাজ ফুরিয়ে যায় না—কারণ, বাংলা ভাষায় ‘যৌক্তিকতা’ শব্দটি এখনো উপর্যুক্ত (কিহানো যে অর্থে ব্যবহার করেছেন) জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা বহন করে না। ‘Rationality’—‘ Reason’-শব্দজাত। ‘Reason’-অর্থে ‘যুক্তি’ শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত। ফলে, ‘যৌক্তিকতা’ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে—যুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সত্তার গুণপনা—the quality of being based on or in accordance with reason or logic। কিহানোর চিন্তায় যে যুক্তি গড়নে–গঠনে আগাগোড়া ইউরোকেন্দ্রিক।
১৩. ইংরেজি ‘epistemology’ শব্দটাকেই আমরা বাংলা করে নিই—জ্ঞানতত্ত্ব। জ্ঞানতত্ত্ব হলো জ্ঞান সম্পর্কিত তত্ত্ব—theory of knowledge। অর্থাৎ, খোদ ‘জ্ঞান’ জিনিসটাই কী? কী প্রকারে তা অর্জিত হয়? এর সীমাবদ্ধতা আছে কি নেই—এইসব নিয়ে তত্ত্ব। দর্শনের অন্যান্য প্রপঞ্চের মতো তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রেও কোনো একক এবং সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত নেই। এই মর্মেই জ্ঞানের প্রশ্নে যুক্তিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের মতো ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের বিকাশ (সরদার, ২০১৭ : ১৫৫)। গোবিন্দচন্দ্র দেব একে ‘ধী–বিদ্যা’ পারিভাষিক নামে পরিচয় করিয়ে দেন। তার ভাষায়, ‘ধী–বিদ্যা ইংরেজী এপিস্টেমলোজী শব্দের বাংলা তরজমা।… জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়, সে জ্ঞানের পরিধি কতখানি এবং সে জ্ঞান সত্যই বিশ্বাস্য কিনা, এইসব প্রশ্নের আলোচনা ধী–বিদ্যায় হয়ে থাকে।… তত্ত্ববিদ্যা [মেটাফিজিক্স্] যে দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত, সমালোচনী মনোবৃত্তি নিয়ে সে দুরূহ কাজ সমাপনের শক্তি আমাদের বুদ্ধির আছে কিনা, তা’ বের করাই ধী–বিদ্যার কাজ (গোবিন্দচন্দ্র, ২০০৪ : ৩৯–৪০)। রমেন্দ্রনাথ ঘোষ এর অনুবাদ করেন—জ্ঞানবিদ্যা (রমেন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ১২৯)।
১৪. বি–উপনিবেশায়নকে আমরা যেভাবেই বুঝতে চাই না কেন, এটি–যে উপনিবেশায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত, এই প্রতিজ্ঞা আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো না। এখন কথা হলো—কীভাবে তা সম্পর্কিত। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কেননা, এই প্রশ্নেই বি–উপনিবেশায়নের চিন্তাগত ফারাকগুলো তৈরি হয়। অর্থাৎ, একেক ধরনের বি–উপনিবেশায়ন একেকভাবে উপনিবেশায়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করে। যেমন, এক–ধরনের বি–উপনিবেশায়ন নির্দেশ করে উপনিবেশিক পর্বের রাজনৈতিক পরিসমাপ্তি। ফলে, এটি নির্দেশ করে কালগত সম্পর্ক। তেমনি, কোনোটি বোঝায় উপনিবেশিক ও উত্তর–উপনিবেশিক দুই পর্বেরই উপনিবেশ–বিরোধী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াই। যা দ্বারা উপনিবেশায়নের সঙ্গে বি–উপনিবেশায়নের পাল্টাপাল্টি সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে, উপনিবেশায়নের সঙ্গে আরেক প্রকার বি–উপনিবেশায়ন স্থাপন করে জ্ঞানতাত্ত্বিক সম্পর্ক। সেই প্রকার বি–উপনিবেশায়ন উপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের পুনর্গঠন নিদের্শ করে। উপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের জবরদস্তির ফলে চাপা–পড়া অপরাপর সমকক্ষ জ্ঞানতত্ত্বের আবির্ভাবকে তা স্বাগত জানায়—এক–প্রকার সর্বজনীনতার বদলে তা দাবি করে কতিপয় সর্বজনীনতা। অর্থাৎ, বি–উপনিবেশায়ন নানা রকমের। সেই সূত্রে উপনিবেশায়নের সঙ্গে বি–উপনিবেশায়নের নির্ধারিত সম্পর্কও অভিন্ন নয়। বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন তত্ত্বও কিন্তু উপনিবেশায়নের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতেই অপরাপর বি–উপনিবেশায়ন চিন্তা থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়ন উপনিবেশায়নের সঙ্গে স্থাপন করেছে সমস্যাকেন্দ্রিক সম্পর্ক। ফলে, উপনিবেশায়ন যেখানে সমস্যা সেখানেই কেবল তা কার্যকর। উপনিবেশায়নের ঢালাও বিরোধিতা তা করে না (মনিরুল, ২০২১ : ১২৬–৭৭)। বাংলাদেশের বিউপনিবেশায়নকে অপরাপর বি–উপনিবেশায়ন থেকে চোখের দেখায় আলাদা করার জন্য হাইফেনের ব্যবহারটাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছি। আমরা হাইফেন ব্যবহার করি না। এর একাধিক কারণ রয়েছে (মনিরুল, ২০২১)। তাছাড়া, শুরুর দিকে অপরাপর ‘ডিকলোনাইজেশন’ হাইফেন সহযোগে অনূদিত হয়েছে—বি–উপনিবেশায়ন। তাই হাইফেন সহযোগে বি–উপনিবেশায়ন বলতে আমরাও অপরাপর ডিকলোনাইজেশনকেই নির্দেশ করি।
সহায়কপঞ্জি
গোবিন্দচন্দ্র, ২০০৪ গোবিন্দচন্দ্র দেব, তত্ত্ববিদ্যা–সার, ঢাকা, অধুনা প্রকাশন।
মনিরুল, ২০২১ মনিরুল ইসলাম, ‘সৈয়দ নিজারের সুলতান পাঠ: প্রসঙ্গ বিউপনিবেশায়ন’, রাষ্ট্রচিন্তা, (সম্পা.) হাবিবুর রহমান, ঢাকা।
রমেন্দ্রনাথ, ২০১৪ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, দার্শনিক প্রবন্ধাবলি, (সম্পা.) হাসান আজিজুল হক ও মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, ঢাকা, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।
রাসবিহারী, ২০১১ রাসবিহারী দাস, কান্টের দর্শন, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।
সরদার, ২০১৭ সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, ঢাকা, প্যাপিরাস।
Gandarilla, García-Bravo
& Benzi, 2021 José Guadalupe Gandarilla Salgado, María Haydeé García-Bravo, Daniele Benz, ‘Two Decades of Aníbal Quijano’s Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America’, Contexto Internacional, Vol. 43 (1)
Maldonado-Torres, 2010 Nelson Maldonado-Torres, ‘On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept’, Globalization and the Decolonial Option, Ed. Walter D. Mignolo & Arturo Escobar, London & New York, Routledge.
Mignolo, 2018 Walter D. Mignolo & Catherine E. Walsh, On Decoloniality, Durham & London, Duke University Press.
James and Adam, 2022 James, Michael and Adam Burgos, “Race”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/race/.
